গা ছুঁয়েই তলিয়ে যাচ্ছে খাদ

সে এক আদিম মহীরুহ, আকাশগঙ্গার থেকেও বৃদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ডে তার এক বিশেষ স্থান আছে। তার বিপুল বপু চলে গেছে সৃষ্টির এক অসীম থেকে অন্য অসীমে। তার চারপাশে গজিয়ে ওঠা ন’টি জগতের অবস্থান আগলে রেখেছে তার সুঠাম শাখাপ্রশাখা। তার শেকড়, তার শাখাপ্রশাখা চারিদিকে ছড়িয়ে, এমন ভাবে সবকিছুকে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে… এই বিশ্বচরাচরের ভারসাম্য এবং শুভাশুভ সব কিছুই তার ওপর নির্ভর করে। সে কখনও স্থির, কখনও দুলে ওঠে সক্রিয় উচ্ছ্বাসে… তার চূড়ায় পেঁজাতুলোর মত তুষার জমে থাকে, শিশির ঝরে পড়ে পাতায় পাতায়। তার শেকড়ের কাছে ভয়াল সরীসৃপদের বাস। ড্রাগন ‘নিডহগ’-এর সঙ্গে তারা চিবিয়ে খাচ্ছে সেই শেকড় অনন্তকাল ধরে। তার সব থেকে উঁচু শাখায় ধৈর্য অভ্যেস করে প্রবীন ঈগল। চার ঋতুর মত চারটি হরিণ, যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিলো তার চিরহরিৎ পাতা খেয়ে।
কাঠবিড়ালী র্যাটাটস্কর একবার ড্রাগনের বার্তা পৌঁছে দেয় ঈগলের কাছে, আর একবার ঈগলের বার্তা পৌঁছে দেয় ড্রাগনের কাছে। একে অপরের প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া শাপ-শাপান্ত এভাবেই বয়ে বেড়াচ্ছে বেচারা। আবহমান কাল ধরে ছুটে চলেছে মহীরুহর আঁচড়-বলিরেখায় ভরা শরীরের ওপর থেকে নীচ, আর নীচ থেকে ওপরে।
এভাবেই স্বর্গ-মর্ত-পাতাল… ত্রিলোকের গভীরে নিজের শেকড় সঞ্চার করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে… তার ক্ষতির ইঙ্গিত ডেকে আনবে সৃষ্টির নাশ। সে, মহাবিশ্বের আদিমতম মহীরুহ — ইগদ্রাসিল।
প্রাচীন নর্ডিক সভ্যতার মানুষদের কাছে ‘দ্রাসিল’ মানে ছিল ঘোড়া। আর ‘ইগর’ মানে ছিল ভয়ঙ্কর। শক্তিশালী নর্স দেবতা ওডিনেরও আর এক নাম ইগর। মহীরুহ ইগদ্রাসিলকেই সমীহ করে বলা হ’ত ওডিনের ঘোড়া।
অথচ বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজনে, দুষ্প্রাপ্য শক্তি অর্জনের স্বার্থে নিজেকেই নিজের কাছে আত্মাহুতি দিয়েছিল প্রবল প্রতাপী ওডিন। আর আত্মহত্যার জন্য মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিল ইগদ্রাসিলকে। নিজেই নিজের বুকে বর্শা গেঁথে ঝুলে পড়েছিল ইগদ্রাসিলের শাখায়।
“I trow I hung on that windy Tree
nine whole days and nights,
stabbed with a spear, offered to Odin,
myself to mine own self given,
high on that Tree of which none hath heard
from what roots it rises to heaven.
None refreshed me ever with food or drink,
I peered right down in the deep;
crying aloud I lifted the Runes
then back I fell from thence.
পৌরাণিক কথা… তার ওপর দেবতা, তার ওপর ওডিনের মত কেউ… তাই ফিরে আসা প্রয়োজন। নিজের প্রত্যাবর্তনের গল্প শুনিয়ে শিক্ষা দিতে হবে অন্য দেব-দেবী ও মানবজাতিকে।
আসলে, এ এক সুপ্রাচীন আত্মহত্যার অলীক গল্প। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে এক অন্য স্তরের ডেস্পারেশনে চলে যাওয়ার গল্প। যেখান থেকে অনেকেই আর ফিরে আসতে পারে না।
— — — —
— বিষ খেয়ে চুপচাপ মরে যেতে পারে… কিন্তু গায়ে আগুন দিয়ে যদি কেউ চুপচাপ মরে, তাহ’লে বলতে হবে এলেম আছে।
— মানে?
— আরে খুন করে, এমন ভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে যাতে মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট।
— না রে… এমন কেস হয়… সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী…
— রাখ! ঘরে ঘরে সব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বসে আছে যেন।
— কেন? বিধুবাবুর কথা মনে নেই? কেউ বুঝতে পারত মেয়ে ঘরে না গেলে?
— কোন বিধুবাবু? বিধান মিত্র? মন্দিরের পাশে তিনতলা বাড়ি ছিল?
— হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ।
— ওটা তো শর্ট-সার্কিট থেকে…
— কচুপোড়া। ওসব বলতে হয়। সারা পাড়া মড়া-পোড়া গন্ধ! তবে অন্য কেউ না, নিজেই…
— দেনা-টেনা হয়ে গেছিল শুনেছিলাম।
— এই দেখ… একটু আগেই বলছিলি শর্ট-সার্কিট।
— আরও কেস ছিল কিছু, ফ্যামিলি প্রবলেম…
— তাই বলছি… হয়, কেউ কেউ থাকে। কীভাবে পারে জানি না। তবে হয়।
— সেই… ঐ ক’বছরের মধ্যে পাড়ায় পর পর যেভাবে মরল…
“তোমরা কী সব নিয়ে কথা বলছ অ্যাঁ? আর কোনও টপিক নেই? ছেলেটাও হাঁ করে গিলছে বড়দের কথা… যা নিজের ঘরে হোমটাস্ক নিয়ে বস! সব সময় বড়দের কথার মাঝখানে বসে থাকা!”
ছেলের হাত থেকে রিমোটটা কেড়ে নিয়ে রীতিমত ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো তনিমা। ড্রয়িং-রুমে বসে থাকা প্রাপ্তবয়স্ক দু’জনের দিকে একটা বিস্ময় এবং ভর্ৎসনা মেশানো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল, যার অর্থ – “তোমাদের কি কোনো আক্কেল জ্ঞান নেই?!”
— মাঝে মাঝে খুব ভয় করে জানো!
— কীসের?
— এই যে ব্লু হোয়েল… মোমো… কী সব হচ্ছে চাদ্দিকে…
— হুম, কিছুটা তো চিন্তারই… কিন্তু এগুলো কেন হচ্ছে জানো?
— এই যে… বাচ্চাকাচ্চাদের হাতে অবধি এই জিনিসটা অবাধে চলে আসার জন্য। কোনও কন্ট্রোল নেই।
‘এই যে’ বলে নিজের বালিশের পাশে রাখা মোবাইল ফোনটা রেখে দিলাম।
— আবার তুমি মাথার কাছে ফোন নিয়ে শুয়েছ? এত করে বারণ করার পরেও… বড়দেরই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, আর বাচ্চারা…
— তাহ’লেই বোঝো। এইসব যে বললে… স্যুইসাইডাল বিপজ্জনক খেলা। কারা ভিক্টিম? কোন এজ গ্রুপ? দেখেছো?
— সেই কারণেই তো বলছি…
পাশের ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে তাকালো তনিমা। ও ঘরেই শোয়ে আমাদের ছেলে বাপান… ভাল নাম সাম্য।
— চারিদিকেই একটা ক্রাইসিস। কোথা থেকে যে কী… যাকগে, রাত্তির বেলা আর এসব ভাবতে ভাল লাগে না। ঘুম বলেও একটা জিনিস আছে। দরকার।
— তোমার বন্ধু অফেন্ডেড হ’ল… না?
— কে? পোনা? ধুস!
— ওভাবে রিয়্যাক্ট করলাম… ভুল করেছি বলো? এগুলো কি বাচ্চাদের সামনে ডিসকাস করার টপিক?
— বাদ দাও তো… কে আমার পোনা, তার আবার মাইন্ড।
— হুম।
— তবে কি জানো?
— কি?
— পোনা কথাটা ভুল বলেনি… সত্যি-ই ওই তিন-চার বছর এমন এক একটা…
— প্লিজ! তুমি আর রাতে শুরু করো না। আমার এমনিতেই রাতে এ’সব শুনলে ভয় করে… অস্বস্তি হয়।
আমাদের পাড়া থেকে কিছু দূরেই একটি পরিবারে ছোটবেলা বেশ যাতায়াত ছিল। বড় পিসির ছাত্র ছিল ওই পরিবারের দুই ছেলে। তখন বড় হয়ে গেছে, তবে ‘দিদিমণি’কে তাদের মা, মাসি বেশ শ্রদ্ধা করতেন। আত্মীয়ের মত হয়ে গেছিলেন। আন্তরিকতার কারণ কিছুটা আধ্যাত্মিকও বটে। আশ্রম, মন্দির… ইত্যাদিতে একসঙ্গে যাওয়ার পরিকল্পনা করত। সেই বাড়ির ভাড়াটে পরিবারের সঙ্গেও মোটামুটি ভালই আলাপ ছিল। ভাড়াটে পরিবারের দুই মেয়ের মধ্যে একজনের নাম ছিল নীলু। নীলুদি না নীলুপিসি, কোনটা বলা উচিৎ বুঝতে পারতাম না। তখন অনেক ছোট। এবং মেয়েটিকে দেখে দিদিদের তুলোনায় বড়ই মনে হ’ত। অথচ তার মা’কে বলতে হ’ত জেঠিমা। তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। মুখ চেনা… ছোট বলে গাল টিপে আদর করত।
একদিন মায়ের সঙ্গে বড়পিসিকে আলোচনা করতে শুনলাম চাপা স্বরে, সিরিয়াস ভাবে। জানলাম নীলুদি হসপিটালাইজড। অ্যাসিড খেয়েছে। ডাক্তার বাহাত্তর ঘন্টা সময় দিয়েছে, অবস্থা ক্রিটিকাল। মা বলল – ‘বাঁচলেও তো সাংঘাতিক কষ্ট!’ তারপর মায়ের পরিচিত একটি মেয়েকে কেমন বিকল্প শব্দযন্ত্র ব্যবহার করে কথা বলতে হ’ত, সেই ব্যাপারে বলল। এমনই একটা বিষয়, যা নিয়ে মা’কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। সেই বয়সে অনুমতি ছিল না। কাউকে বুঝতেই দেওয়া যেত না, যে কথাগুলো আমিও শুনছি।
ক’দিন পর বড়পিসি ব্যাংক থেকে ফিরে জানাল – নীলু মারা গেছে।
সেই প্রথম কারও আত্মহত্যার খবর পেলাম। অথচ, নীলুদি বা নীলুপিসি কেন অ্যাসিড খেয়েছিল অনেক আড়ি পেতেও তা আর জানতে পারিনি। জিজ্ঞেসও করা হয়নি।
পোনা ঠিকই বলছিল, কয়েক বছরের মধ্যে পাড়ায় সত্যিই বেশ কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল। অস্বাভাবিক মৃত্যু। পাড়ার মোড়ে সাইকেল সারানোর দোকান। সেই দোকেনের বুড়ো মালিকের ছেলে সাইকেলের চেন গলায় বেঁধে ঝুলে পড়েছিল। রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরেনি। সকালে সবাই এসে দেখেছিল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজা ভাঙতে দেখা গেল ননীদা ঝুলছে। না… আমি দেখিনি। স্কুল থেকে ফিরে খবরটা শুনলাম। ততক্ষনে বডি নিয়ে গেছে পোস্টমর্টেমের জন্য। ছোটবেলা ‘পোস্টমর্টেম’ শব্দটা শুনলেই গা ছমছম করত। একটা রহস্যমাখা ব্যাপার। একজন আত্মীয় জিজ্ঞেস করেছিলো, “তোদের পাড়ায় নাকি সুইসাইড করেছে?” বলেছিলাম – জানি না। সেটা আবার আমার মাকে নালিশ করেছিল “তোমার ছেলে এত মিথ্যে কথা বলে কেন?” ননীদার মত ভদ্র, শান্ত ছেলে হঠাৎ কেন গলায় চেন দিয়েছিল, বুঝতে পারিনি। আমার সামনে বা আড়ালে এই নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি বাড়িতে। ননীদার ছবিটা দোকানে ঝুলত। মাঝে মাঝে ছেলের ছবির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত ননীদার বাবা… দোকানের বুড়ো মালিক – নামটা এখন আর মনে পড়ে না। বোধহয় কেষ্ট। আসলে, পাড়ায় শিবমন্দিরের পুরোহিতের নামও কেষ্ট ছিল। কেষ্টদাদু। তাই নিশ্চিৎ মনে পড়ে না। ননীদার বাবার নাম নারাণও হ’তে পারে। ননীদার ভাই টিংকাদাও দোকানে বসত, বাবাকে সাহায্য করত। সবাই বলত ননীর ভাই ফনী। কিন্তু খুব একটা দেখা যেত না। ননীদা মারা যাওয়ার পর ওই টিংকাদাই দায়িত্ব নিয়ে নিলো। ননীদার স্যুইসাইডের ব্যাপারটা প্রায় ফিকেই হয়ে গেছিল যখন পরের খবরটা এলো… টিংকাদাকে কারা মার্ডার করে দিয়েছে! টিংকাদাকে ক’দিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর অন্য অঞ্চলে একটা ঝিলের ধার থেকে পেয়েছিল বডি। বস্তা বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছিল, আততায়ীরা অ্যাসিড ঢেলে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বাবা এইসব কথা ঘরে বলার জন্য বড় পিসির কাছে ধমক খেয়েছিল। আমি শুনে শিউরে উঠেছিল – “চামড়া খসে খসে পড়ছে, বডি তুলতে পারছিল না।” এই দেহ ওখান থেকে মর্গে চলে যায়, আর পাড়ায় ফেরেনি। টিংকাদা কেন খুন হ’ল… তা আর জানা গেল না। যে যার নিজের মত গল্প ভেবে নিয়েছিল। তবে মুখে আলোচনা করত না… পুলিশ এসেছিল দু-তিনবার পাড়ায়। সাইকেল দোকানটা বন্ধ ছিল অনেকদিন। তারপর যখন খুলল, ননীদার বাবার মুখের দিকে তাকানো যেত না। এক বছরের মধ্যে দুটো ছেলের অস্বাভাবিক মৃত্যু লোকটাকে জীবন্মৃত করে দিয়েছিল। পেটের টানে দোকান চালাতো। হাঁটতে গেলে পা কাঁপত… ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত রাস্তার দিকে, ঠোঁটের কোণে এক অব্যক্ত বিরক্তি নিয়ে।
অনেক রাতে বন্ধ দোকানের পাশ দিয়ে গেলে মনে হ’ত ভেতরে একটা সাইকেলের চেন ঝুঁলছে সিলিং থেকে। এখনও ঝুলছে।
— খবরের কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দেবো।
— কেন?
— ফালতু টাকা নষ্ট। শুধু খুন-খারাপির খবর আর বিজ্ঞাপন।
— খবরের তো অতটুকুই রয়ে গেছে। টিভিতেও তো একই…
— হ্যাঁ, এই একই টিভিতেও দেখায়। পেপার নিয়ে কী হবে? ছেলেও বাংলা কাগজ পড়ে না। বাড়িতে দু-দুটো কাগজ আনা হচ্ছে। ইংলিশটা পড়? তাও পড়ে না। তারপর যা সব ছবি ইংরিজি কাগজগুলোতে!
— সে কি আর তোমার আমার হাতে? সংবাদ মাধ্যম এখন বিনোদন মাধ্যম। যে যেমন টাকা দেয়…
— তাই যেটা হাতে আছে, সেটাই করছি। কোনও দরকার নেই দু-দুটো কাগজ কিনে বাবুয়ানি করার। ইংলিশ স্কিল বাড়ানোর হয়, ছোট ছোট ইংরিজি গল্পের বই পড়ুক। অডিও শুনুক।
— ছেলে বড় হচ্ছে, ঘরে বাইরে অনেক কিছুই এখন চোখে পড়বে। কত দিক দিয়ে আটকাবে বল তো?
— জানি না… দিন দিন সব উচ্ছুন্নে যাচ্ছে। কী সব ভাষা, কী সব পোশাক-আশাক। দেখ তুমি… ফ্রন্ট পেজ… পুরো পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন। পরের পাতা থেকে খবর শুরু। হেডলাইন কৃষকের আত্মহত্যার খবর। এই ভাবে দিন শুরু হবে রোজ?
— তুমি হাসছ? স্ট্রেঞ্জ!
— একটা কৃষকের আত্মহত্যা… কতগুলো জীবন একসাথে শেষ হয় জানো? কতগুলো দিনের শুরুটা বদলে গেল জানো?
— ঘুম থেকে উঠে তোমার খবরটা দেখে বিরক্ত লাগছে। ভাবো তো… এই খবরগুলোই এত বেশি করে দেখতে হচ্ছে কেন?
— দেখো!… এমন খুন, স্যুইসাইড আগেও হ’ত। খবরে দিলেও ভেতরের পাতায়…
— সেই সব খবর হেডলাইন হয়ে যাচ্ছে। ক্রাইসিসটা বুঝতে পারছ?
— আমি বুঝে কী করব? আমাদের বুঝে কী হবে? যাদের বুঝলে কিছু হবে তারা বুঝুক!
— সেই…
পূর্ব জার্মানীতে এক গোপন পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল ‘৫১১ কিন্ডারহাইম’ নামের এক অনাথ আশ্রমকে। উদ্দেশ্য ‘পারফেক্ট সোলজার’ তৈরি করা। অনাথ আশ্রম থেকে উপযুক্ত বালকদের বেছে নিয়ে তাদের একের পর এক বিশেষ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে মানসিক-শারীরিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এক শীতল ও ক্রূর পিশাচে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা। পরীক্ষামূলকভাবে সে কাজ সফল হ’লে এভাবেই একের পর এক নর-পিশাচ সৃষ্টি করে নেওয়া হবে… তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হবে চারিদিকে। এক একজনকে এক একরকম ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করতে প্রয়োগ করবে রাষ্ট্র।
একদিন হঠাৎই সেই অনাথ আশ্রমের ডিরেক্টর অস্বাভাবিক ভাবে মারা গেলেন। এবং তারপর এক আতঙ্কের পরিবেশে অনাথাশ্রমের প্রত্যেকে একে অপরকে খুন করে শেষ হয়ে গেল। বড় ছোট সবাই। কেবল একটি ছেলে আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গেল। ছেলেটির নাম যোহান।
যোহানের মধ্যে এক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ছিল, মানুষকে ঠাণ্ডায় মাথায় প্রভাবিত বা সম্মোহিত করে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার। তার মনে কোনও অনুতাপ ছিল না। ছোটবেলা থেকেই সে চাইত, পৃথিবীর শেষ জীবিত ব্যক্তি হিসেবে টিকে থাকতে… প্রয়োজনে সবাইকে শেষ করে। তার মস্তিষ্কই তার সব চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। সেই ক্ষমতা কাজে লাগিয়েই সে একের পর এক হত্যা করত। সেইসব হত্যাগুলির বেশিরভাগই দেখে মনে হ’ত অন্য কারও দ্বারা সুপরিকল্পিত হত্যা, অথবা আত্মহত্যা। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন এক ঠাণ্ডা মাথার অপরাধী… ‘পারফেক্ট সোলজার’এর থেকেও সাংঘাতিক এক দানব। তাকে ধরা, তাকে থামানো বা তাকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা… সব কিছু যেন সিস্টেমের সাধ্যের বাইরে চলে গেল; কারণ সে নিখুঁত, সে অন্যদের থেকে উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী। একদিকে তাকে থামাতে যেমন কিছু ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েছিল, তেমন অন্যদিকে তাকে ব্যবহার করে আবার ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল কিছু লোক।
সেই ঠান্ডা মাথার জিনিয়াস অপরাধী যোহানকে ধরার জন্য পথে নেমেছিল একজন শল্য-চিকিৎসক, যে নিজেই একদিন তাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে। সেই চিকিৎসকের একমাত্র ভরসা ছিল যোহানেরই যমজ বোন, এর এক অনাথ… নিনা। ‘নিনা’র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও দুঃস্বপ্ন আছে। দুই ভাই-বোন বহন করে চলেছে মানসিক ক্ষত। আসলে, তারা কেউই সে অর্থে অনাথ নয়… তাদের মা চরম বিপদের মুহূর্তে বেছে নিয়েছিল দুজনের মধ্যে একজনকে… জ্ঞানত, অথবা অজ্ঞাত ভাবে।
এমনই একটি প্রেক্ষাপটের ওপর নির্মিত নাওকি উরাসাওয়ার জাপানী অ্যানিম — ‘মনস্টার’ । বার বার সেই প্রশ্ন ভেসে আসে দর্শকের সামনে আসলে ‘মনস্টার’ কে?
যোহানের মতই, পরিস্থিতি বা সিস্টেম বা সিস্টেমের এক একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে বসে থাকা কিছু মানুষ এমনই আত্মকেন্দ্রিক এবং সুবিধেবাদী ‘মনস্টার’ হয়ে উঠেছে। যোহানের মতই এরা নিজেদের প্রতিশোধ স্পৃহা বা সেলফ-রাইটিয়াসনেসকে জাস্টিফাই করতে পারে। অন্যদের বুঝিয়ে দিতে পারে যেতে এই সিদ্ধান্তেই সকলের মঙ্গল — জাতির মঙ্গল, বৃহত্তর স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় কাউকে না কাউকে। এদের পরিকল্পিত পদক্ষেপের ফলশ্রুতি কোথাও হতাশা, কোথাও নৈরাশ্য, কোথাও আত্মহত্যা। কৃষক, দলিত, শ্রমিকদের এক একটা আত্মহত্যার খবর শুনে মাঝে মাঝে যোহানের কথা মনে পড়ে। কেউ কোথাও পরিকল্পিত হত্যাই এমন ভাবে ঘটাচ্ছে… আমরা দেখে সবাই বলব আত্মহত্যা। একটা মৃত্যু, একটি জীবন বা পরিবারের শেষ হয়ে যাওয়াকে ‘আত্মহত্যা’ বলে দিতে পারলেই একসাথে অনেকগুলো চ্যাপ্টার ক্লোজ করে দেওয়া যায়। সে দায় আর অন্য কারও নয়।
তাহ’লে কি আমাদের শাসনযন্ত্রের মধ্যেই এভাবে ‘পারফেক্ট সোলজার’ তৈরী করে দেওয়া হয়েছে?
— আর কোথায় কোথায় সিসিটিভি রাখবে বলো তো?
— রেখেই বা কী হবে? দরকারের সময় তো ফুটেজ পাওয়া যায় না।
— পেলেও দেবে না। দিলেও তুমি-আমি জানব না ওতে কী ছিল।
— সেই…
— ভাবতেও কেমন লাগে… একটা বাচ্চা মেয়ে, স্কুলে পাঠিয়েও বাবা-মার শান্তি নেই!
— একসাথে তিনটে স্কুলের নাম এসেছিল… তারপর… ফুসসসসসস। কে কেমন আছে… কার কী হ’ল… কিচ্ছু জানি না!
— মাঝখান থেকে একটা সিনেমার ভেতর ক্যাপসুল বানিয়ে গিলিয়ে দিলো – এসব কিছুই হয় না, সব বাবা-মা’র অতি-প্রতিক্রিয়া… ওভার-রিয়্যাকশন।
— হা হা হা হা… শুধু মা’দের বললে ঠিক ছিল। মা’রাই তো সব গেম-চেঞ্জার!
— থামো তো! ছেলেটা একা একা স্কুলে যায়, পড়তে যায়… বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত একটা অস্বস্তি হয়! দুশ্চিন্তার থেকেও বেশি অস্বস্তি।
— আমাদের ছোটবেলা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে থাকত গলির মুখে। কালো পুলিশ ভ্যান। বাবা পাশ কাটিয়ে ঢুকত অফিস থেকে ফেরার সময়। বলেছিল কারও চোখের দিকে না তাকাতে। কথা কম বলতে।
— কফি খাবে? আমার কফি তেষ্টা পাচ্ছে…
— একা খেতে অসুবিধে হবে বলে সাধছো?
— ঢং করো না তো…
— তোমার দাদা একবার অ্যারেস্ট হয়েছিল না?
— অ্যাঁ… দাদা কী বলেছিল?
— আরে অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট… অ্যারেস্ট হয়েছিল তো একবার!
— ধ্যাত! ওটাকে আবার অ্যারেস্ট বলে নাকি… স্টুডেন্টস ইউনিয়ন করত, প্রোটেস্ট র্যালি থেকে তুলে নিয়ে গেছিল সব গাড়িতে ভরে। সন্ধেবেলা ছেড়ে দিয়েছিল।
— গ্রেফতারের গল্পটা এখনও যেভাবে করে… ছাত্র আন্দোলন… বাবা!
— বেশ করে… অ্যারেস্ট হয়েছিল, তাই বলে! নাও ধরো।
— এসএফআই করত না ডিওয়াইএফআই… না অন্য কিছু?
— হঠাৎ দাদাকে নিয়ে কেন পড়লে বলো তো?… দাদাকেই জিজ্ঞেস করতে পারো তো এসব।
— না না… ওই কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল।
— আমি তো খুবই ভীতু ছিলাম।
— সে আর আমার চেয়ে ভাল কে জানবে!
— দরকারের সময় সাহসও দেখিয়েছি… দেখাইনি?
— ছাড়ো!… আসলে দাদাও ওই দলে ভিড়েই… এখন লোকজনকে সেই সময়ের ছাত্র-রাজনীতি এসব বলে বটে… অদ্ভুত রোম্যান্টিসিজম!
— মে বি… তবে… দাদার কিছু বন্ধু খুব সিরিয়াস ছিল জানো তো। একজন পার্টিতে ভালই জায়গা করে নিয়েছিল। আর একজন…
— আর একজন?
— জানি না গো… এখনও বুঝি না। কী যে হ’ল হঠাৎ… একদিন শুনলাম রিস্ট স্লিট করেছে…
— কী যে ভাল মানুষ… কী ভাল কথা বলতে পারতো, ডিবেট করতে পারতো… একদম ফ্রণ্টে থাকত মিছিলের। একদম সিনেমায় যেমন দেখায়, পাঞ্জাবী, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ… খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খুব স্নেহ করত আমাকে।
— কই আগে তো কখনও বলোনি ওনার কথা?
–
— কী আর বলব… হঠাৎ মনে পড়ে গেল।
— হুম।
— আমাদের বিয়ের দু বছর আগে… দাদা বাবা সবাই খুব শক পেয়েছিল। একটা ঝকঝকে ব্রাইট ছেলে। কী বোকার মত কাজ! কার লাভ হ’ল এটা করে?
— সাবকনশাস।
— অ্যাঁ?
— হয়ত এই কারণেই তুমি সেদিন স্যুইসাইডের কথায় আনকমফোর্টেবল ফীল করছিলে।
— না না… ধ্যাত। সে কত বছর আগের কথা। আমাদের বিয়েরও আগের… বুঝতে পারছ?
— সাবকনশাস এভাবেই থেকে যায়। মাঝে মাঝে উঁকি দেয়।
— না… এই অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের সাডেন ডিসিশন, হঠাৎ একটা ড্রাস্টিক স্টেপ নেওয়া… এই ব্যাপারগুলো আমার ইরিটেটিং লাগে। লুজার!
— তোয়া চ্যাটার্জী, রোহিত ভেমুলা, অনিতা শনমুগম… এই লুজারগুলো কেন হেরে যায় বলো তো? কাদের কাছে হেরে যায় এরা? কারা হারায় এদের?
— ভাল লাগছে না… লীভ ইট। ছেলেটা আসছে কি না দেখি বারান্দায় গিয়ে… আসবে?
— বারান্দায় যা মশা।
— হোক গে… এসো না… ঘরের ভেতরটা কেমন…
— আচ্ছা… চলো। দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাও, ঘরে মশা ঢুকবে।
— বাপান?
— বাপান… একবার শুনে যা এদিকে…
— কী হ’ল কী? ডাকছি তো…
— আসছি… বলো।
— পাশের ঘরে আছিস… ডেকে যাচ্ছি। সারা দিতেও অসুবিধে? কী করছিলি কী?
“ডেকে সারা পাওয়া যায় না… বললে কথা কানে যায় না… ইচ্ছে হলে শোনে না হলে শোনে না… বাড়িতে শাসন না থাকলে যা হয়!”
কথাগুলো বলতে বলতে বারান্দা থেকে কাপড় তুলে বেডরুমের দিকে চলে গেল ওর মা। মায়ের ওই চলে যাওয়া দেখতে দেখতে বাপান উদাসীন ভাবে বলল “বলো”।
আমার মুশকিল হ’ল আমি ওর মাকে যতটা রাগের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারি… সেটা বাপানের সামনে পারি না। রাগ হলেও গলা তুলতে পারি না ওর মায়ের মত। ছোটবেলা কেউ বেশি চেঁচালে, ধমকালে তার প্রতি একটা বিরক্ত চলে আসত। বাপানের চোখে সেই বিরক্তিটা এলে আমি ঠিক বুঝতে পারব। তাতে অস্বস্তি বাড়বে। মনে মনে বিরক্ত হয়েও ঠান্ডা ভাবে বললাম – “এদিকে আয়, কথা আছে…”
— প্রোজেক্টের কাজটা কিন্তু পড়ে রইল… এরপর মা চ্যাঁচাবে, তুমিও মায়ের সাইড নেবে তখন।
— কোন প্রোজেক্ট… হিস্টরির?
— না জিয়োগ্রাফি।
— প্রিন্ট আউটগুলো তো নিয়ে এলাম… এবার স্যাটাস্যাট লাগাবি আর লিখবি।
— সেটা কে করে দেবে? তুমি?
— হ্যাঁ… রাতের দিকে বসব।
“তাহ’লেই হয়েছে”, অস্ফুটে কথাগুলো বলে রান্নাঘরে চলে গেল তনিমা। বাপান শুনেছে, বুঝতে পারলাম।
বললাম, “ঠিক আছে, এখনই চ… দেখি একসাথে কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু আগে অন্য একটা কথা বল…”
বলতে বলতেই দু’জনে উঠে পড়ে ওর ঘরে পড়ার টেবিলের দিকে চলে গেলাম। ঘরে ঢুকে প্রিন্ট-আউটগুলো একধারে রাখতে রাখতে বললাম, “এবারে বল তো… তীর্থর কেস টা?”
— কোন কেস?
— স্মার্ট ফোন নিয়ে ক্লাসে যাওয়ার জন্য তীর্থর গার্জেন কল হয়েছে? ফোনটা কেড়ে নিয়েছে?
— হুম।
— বলিসনি তো।
— কী রে?
— আরে তীর্থর মোবাইল কেড়ে নিয়েছে তো আমি কী বলব?আশ্চর্য।
— আর তুই আমাদের এক্সট্রা ফোনটা যে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে গেছিলি?
ইচ্ছে করেই গলাটা নামিয়ে বললাম, যাতে ওর মা শুনতে না পায়। বাপানের মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চুপ করে অন্য দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কানের পাতা লাল হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পেলাম। কেমন ছটফট করে নিজের পক্ষে কিছু বলতে শুরু করতেই আমি ইশারায় বললাম, ‘আসতে… ফোনটা যে নিয়ে গেছিস তা আমি দেখেছি। তুই ব্যাগ থেকে বার করে টেবিলেই রেখে দিয়েছিলি রাতে। ড্রতে জায়গা মত রাখতে ভুলে গেছিলি।’
— ওতে তো সিমও থাকে না, চার্জও থাকে না! চার্জারও জানি না, কোথায় রাখা…
— তাহ’লে নিয়ে গেছিলি কেন?
— চার্জার আর সিম… এই দুটো অন্য ফোনেরও ব্যবহার করা যায় বাপান। এই স্মার্টফোন বাজারে আসেনি… তবে থেকে ফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। তোদের মত স্কুল-লাইফে ফোন পাইনি। বাড়িতে ল্যান্ডলাইনই ছিলো না তো মোবাইল ফোন।
— কী করছিলি ফোন নিয়ে… বল? সত্যি কথা বললে ব্যাপারটা বেশি দূর এগোবে না।
— তাহ’লে এবার থেকে সব কিছু আলমারীতে লক করে রাখব? চাবিটাও লুকিয়ে রাখব? ঘরের মানুষকেই বিশ্বাস করা যাবে না?
বাপান অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, চোয়াল শক্ত… চোখের কোণ চিকচিক করছে। এটা ওর মায়ের স্বভাব।
— বল?… কী করিস তোরা ফোন দিয়ে? গেম খেলিস? চ্যাট করিস… সিম কে আনে?
— স্কুলে নিয়ে যাইনি।
— তাহ’লে?
— কোচিং-এ।
— কেন?
— সবাই আনে। গেমিং গ্রুপ আছে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে।
— দেখ, এই ফোনটা অন করে নেটোয়ার্ক অ্যাক্টিভেট করলেই সব জানতে পারব কী কী করা হয়েছে। কিন্তু তুই জানিস, পার্সোনাল স্পেস-এ আমি ঢুকি নি কখনও। তুই যা করছিস… করেছিস… ট্রাস্ট করেছি তোকে আমরা। কেন লুকোচুরিগুলো করছিস? এগুলো মা জানলে আপসেট হবে না?
— ঠিক আছে, তুমি ফোন রেখে দাও। আমি আর নিয়ে যাব না।
— সে তো যাবি-ই না। দেখলেই আটকাবো। যেটা নিজের মা-বাবাকে লুকিয়ে করতে হয়, সেটা না করাই ভাল। সে বয়স এখনও পড়ে আছে। যাক গে… বলছি তোর যে গেমিং গ্রুপ বা অন্য গ্রুপ বলছিস – কম্পিউটারে হবে না? ঘরে ফিরে ডেস্কটপে বসে খেল… কোচিং-এ নিয়ে যাওয়ার কী আছে?
— আরে ও তুমি বুঝবে না। অ্যাপ থাকে ফোনে। কম্পিউটারে হবে না, হলেও অনেক ঝামেলা।
— একটা কথা জিজ্ঞেস করছি… একদম সত্যি বলবি। ওকে?
— কী?
— কতদিন হ’ল লুকিয়ে ইউজ করছিস স্মার্ট-ফোনটা ?
— পুজোর আগে থেকে।
— কত আগে?
— ওফ… জানি না, যাও তো!
— বাপান!
— ওই সেপ্টেম্বার হবে।
— সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এ তোকে টেন পাশ করার আগে আমি ঢুকতেই দেবো না। সে অ্যাপ হোক আর যা-ই হোক। তাতে যে যা খুশি বলুক আমায়। তারপর ভাল-মন্দ যা করবি… নিজে বুঝবি, নিজে ভুগবি।
— হুম।
— কী হুম… যেটা বললাম, শুনবি তো?
— হুম।
— আর এই নিয়ে ডেয়ারিং করে কিছু প্ল্যান করতে যাস না। পড়াশুনোটা ডকে উঠবে… সামলাতে পারবি না… সবার প্রবলেম।
— হুম।
— আর একটা কথা… কেউ কিছু কাজ দিলে, বা কিছু করতে বললে… তাতে যতই মজার কিছু বা দারুণ কিছু ঘটার হোক, পাওয়ার থাকুক… এমন কিছু করিস না, যা তুই আগে করিস নি বা করতে জানিস না। আর এমন কিছু করতে বললে একবার মা’কে বা আমাকে জানাস। চেপে যাস না। অস্বস্তি হলেও জানাস। আমার হয়ত কষ্ট পাবো, কিন্তু ক্ষতিটা তোর হবে। নিজের ক্ষতিটা দিনের শেষে নিজেরই ক্ষতি।
বাপান কতটা শুনলো আর কতটা মানবে বুঝতে পারলাম না। মুখ গোঁজ করে বসে রইল। বড় হচ্ছে, অভিযানে বাধা পেলে এই প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। অথচ, এই ব্যাপারটায় একেবারে ছেড়েও দিতে পারলাম না।
“দুজনে এতক্ষণ ধরে দরজা ভিজিয়ে কী গুজগুজ করছ বলো তো? ব্যাপারটা কী?”
দরাম করে তনিমা দরজার পাল্লাটা ঠেলে খুলে দিলো। দুজনেই চমকে উঠলাম। বাপান একটু বেশিই চমকে গেছিল মা হঠাৎ ঢুকে পড়তে।
আমি বললাম – “ওই… ভাবছিলাম বাপানের নামে একটা এফবি অ্যাকাউন্ট থাকলে ভাল হয়… ওটা আমিই অপারেট করব। ও ইলেভেনে উঠলে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার মত ওটার পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো। কিউট ব্যাপার না?”
তনিমা তার পরিচিত অবিশ্বাস আর বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।
বাপান কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দেখল… কথার ফাঁকেই ওর অনেকগুলো প্রিন্ট আউট আমি সাইজ করে কেটে খাতায় জায়গা মত বসিয়ে দিয়েছি। অস্ফুটে বলল ‘হেবি তো’।
— একটা কথা বলছি… উত্তেজিত হয়েও না।
— আর নতুন করে কীসেই বা উত্তেজিত হবে!
— সিরিয়াস ব্যাপার।
বলে তনিমা উঠে বসল।
আমি উঠলাম না। শুয়েই জিজ্ঞেস করলাম… কী ব্যাপার?
— বাপান লুকিয়ে স্মার্ট ফোন ইউজ করছিল… জানো? আমি হঠাৎ করে কিছু বলতে পারিনি। মানে বলিনি আর কী… দেখব ফোনে কী আছে, কী করে ফোনটায়… সিমই বা কোথায় পাচ্ছে বলো? ফোনটায় তো সিম নেই!
— জানি।
— কী জানো?
— ওই বাপানের ব্যাপারটা।
— বলোনি তো?
— ওই… তুমিও জানতে, আমিও জানতাম। আগে বলা হয়নি। এখন কথা হচ্ছে।
— কী করা যায় বলো তো। স্মার্ট-ফোন মানে তো অস্ত্র তুলে দেওয়া হাতে। নিজের ক্ষতি করে ফেলবে… এটাই তো ফাঁদে পড়ার বয়স। যা বোকা ছেলে!
— ব্যাপারটা বোকা চালাকের নয়… সময়টাই খারাপ। খুব খারাপ। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গুলোতে, ফেসবুকের পেজ আর গ্রুপগুলোতে… যা চলে। যা সব পোস্ট হয়। আগে ছিল অবসিনিটির ভয়, ছেলে পেকে যাবে। এখন সব ক্রিমিনাল… অসামাজিক কীট এক একটা! কী সব কথা, কী সব ভাষা। হিউম্যানিটি আর হিউমিলিটি… দুটোই শেষ।
— এই শোনো… কার কী হল না ভেবে ছেলেটার কথা ভাব। কী করা যায় বলো।
— কথা বলেছি…
— কখন? ওই প্রোজেক্ট করার নাম করে…
— হুম।
— স্বীকার করল? জানাল কী করে ফোন নিয়ে?
— হ্যাঁ… গেম খেলে। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ… এইসব করে। ওই যেমন আজকাল সব স্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়েরাই করছে। সবাইকেই তো দেখছে… তোমার দাদার মেয়ে, আমার দিদির ছেলে-মেয়েরা… একা ওকে বারণ করলে শুনবে কেন?
— শুনবে কেন মানে? ওর বয়স হয়েছে এসবের? কত রকম কন্টেন্ট… গেমগুলোই তো কেমন অস্বাভাবিক লাগে।
— তুমি গেম খেলো?
— ধ্যাৎ!… দেখি তো অ্যাড গুলো। ইশ! ওগুলো গেম?!
— আমাদের ছোটবেলা সব ব্যাপারে এত জটিলতা ছিল না। ওই সন্ধের পর বাইরে থাকতে বারণ করত, দুপুর-রোদে ছাদে যেতে বারণ কর, চা থেকে সিগারেট সব কিছুই বড়দের বলে ধমকে দিতো, আর মাঝে মাঝে বিশেষ কারো সাথে মিশতে বারণ করত। বারণ না শুনলে এক দফায় ঝেরে শিক্ষা দিয়ে দিতো। আমরাও কেমন ভয়ে ভয় কলেজ অবধি চলে গেলাম।
— সেই… আমরা কলেজেও গেছি ভয়ে ভয়ে। মনে হ’ত বেচাল করলে ঘাড় ধরে কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে… লেখা পড়া শেষ।
— অন্য রকম চিন্তা হয় এখন… কী থেকে দূরে রাখব, কোনটা বারণ করব। বারণ করেও কত দিন দূরে রাখতে পারব… কিছুই বুঝতে পারি না!
— আর কী ভাবে বারণ করব বলো তো। ফোনের ব্যাপারটা নিয়ে না হয় আজ কথা হচ্ছে… আর কত কি আছে। কত কিছু এমন লুকিয়ে চলবে… আমরা টেরও পাব না। বড় হচ্ছে… নিজের বুদ্ধি হচ্ছে, কৌতূহল বাড়ছে। বাইরে থেকে বদবুদ্ধি দেওয়ার মত স্পয়েল্ট ছেলেমেয়েদেরও অভাব নেই!
— হুম, ওই কৌতূহল খুব সাংঘাতিক জিনিস। বারণ করলেও জেদ আর কৌতূহল বেড়ে যায়। বোঝাতে হবে ঠান্ডা মাথায়… বুঝলে?
— বুঝি… আমাদের কেউ এত কিছু বোঝায়নি। ভাবতই না। কিন্তু আমাদের বোঝাতে হবে। কিছু বারণ করলে তো জানতে চাইবেই কেন…
— ঠিকঠাক কারণ বলাও বিপদ।
— এই যে ব্লু হোয়েল… মোমো… এইসব বিভৎস বিপজ্জনক ঘটনা। জানলেই তো ডিটেলস জানতে চাইবে।
— শুনেছেও এর মধ্যে… হয়ত জানেও। আজকাল ছেলেমেয়েরা খুব অ্যাডভান্সড।
— সেটাই তো ভয়ের। টেনশনের।
— টেনশন করে ব্লাড সুগার আর প্রেশার ছাড়া আর কিছু বাড়বে না। এই নিয়েই চলতে হবে। আমাদেরই মাথা ঠিক রাখতে হবে। আজ বলেছি কথা, তুমি এর ওপর আর কিছু বলো না। শুধু মোবাইলটা সরিয়ে রাখব ক’দিন।
— যদি গোঁ ধরে…
— অন্য রকম ভাবে সামলাতে হবে। সেরকম হলে তোমার বা আমার ফোনটা কিছুক্ষণের জন্য দেব গেম খেলতে। টেস্টে ভাল রেজাল্ট করলে ওর জন্য এক্সট্রা নেট প্যাক ভরে দেবো। ওয়াইফাই ব্যবহার করতে দেবো।
— তোমার এসব বেশি চালাকির বুদ্ধি… সব কিছু এমন স্ট্র্যাটেজি খাটিয়ে চলে না।
— দেখি না… রেজিস্টেন্স তো একটা রাখতে হবে। ওর বয়সী ছেলে আজকাল নেট-এ সার্চ করতে শুরু করলে কোথা থেকে কোথায় যেতে পারে তুমিও জানো আমিও জানি। সব কি আর আটকাতে পারবে? রেজিস্টেন্সটা দরকার।
— হুম বুঝেছি… পিজি।
— কী?
— ওই সিনেমায় যেমন লেখা থাকে পেরেন্টাল গাইডেন্স। ওই ভিজিলেন্স চালিয়ে যেতে হবে।
— কী হ’ল?
— কিছু না
— হঠাৎ চুপ করে গেলে?
— ওই ভাবছি… আমাদের মত অন্য বাবা-মাও তো কিছু না কিছু ভেবে রাখে। বোঝানোর চেষ্টাও করে। বোঝারও। তাও দেখো… কী থেকে কী হয়ে যায়।
— প্লিজ! রাতের বেলা এইগুলো আর টেনো না।
— ওরকম একটা দুটো ঘটনা ঘটে। সবার নিশ্চয়ই এমন হবে না। এসব উইক… দুর্বল মনের ছেলে-মেয়ে। নাহলে এমন করত না!
— ওভাবে বাইরে থেকে সব বোঝা যায় না। মুহূর্তের সিদ্ধান্ত। কত রকম ঘটনা আছে জানো? অবিশ্বাস্য মনে হবে শুনলে। দুর্বলতা নয়… অবসাদ, বিষাদ্গ্রস্ততা, একাকীত্ব, ইনসিকিওরিটি… আরও কত রকম মেন্টাল কন্ডিশন আছে… স্কিৎজোফ্রেনিয়ার বা ক্রনিক ডিপ্রেশনের মত অসুখ আছে… খারাপই লাগে ভাবলে।
— আমার এসব ভাবলেই মাথা ঝিমঝিম করে… একটু জড়িয়ে ধরো। একা একা লাগছে খুব।
মানসিক অসুস্থতা এবং আত্মহত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো সত্যিই তনিমাকে হন্ট করে। কার্ট কোবেনের পোস্টারটাও ও ছেলের ঘরে রাখতে দেবে না, যদি ওকে বলি কোবেনের আত্মহত্যার কথা। ওভার অ্যাক্টিং বা ন্যাকামো নয়। কথা থামিয়ে ওকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে শুয়ে থাকাটা সত্যিই দরকার। আসলে এই দু-তিনদিন ধরে তনিমার একটু তাড়াতাড়ি টেম্পার লুজ করাটাও একরকম মানসিক অস্থিরতা থেকেই। বাপানের স্কুলে ক্লাস ইলেভেনের ছেলেটির স্যুইসাইডের ব্যাপারটায় অনেক অভিভাবকই শক্ড। তবে তনিমা একটু বেশিই মাথায় নিয়ে ফেলেছে ব্যাপারটা। আমি বুঝতে পারছি। নাহ’লে পোনার সামনে ওভাবে মেজাজ হারাতো না। ওটা ওর স্বভাব নয়। বরং ছেলেকে টেনে নিয়ে চুপচাপ অন্য ঘরে চলে যেত। আমাকে ইশারা করত টপিক চেঞ্জ করতে। তনিমাকেও দোষ দেওয়া যায় না… এগুলো ওকে এফেক্ট করে। আর একটা বাচ্চা ছেলের ব্যাপার। এমন একটা কেনই সিদ্ধান্ত বা নেবে? কেউ কেউ বলছে ব্লু হোয়েল কেস। ওর বাবা-মা অবশ্য সেসব বলেননি। বাবা খুবই ভেঙে পড়েছেন শুনলাম… মনে হ’ল কারণটা বলতে চাইছেন না বলেই ‘বুঝতে পারছি না’ বলছেন। পারিবারিক ইন্টারনাল ব্যাপার – বাইরে থেকে বোঝা খুব মুশকিল। সন্তানের বাঁধানো ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা আজীবনের শাস্তি।
কত মানুষ এক বিশেষ মুহূর্তে শুধু চায় তাকে কেউ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকুক… পায় না।
কোথাও কেউ খবর দেখতে দেখতে বলে – দুর্বল মানসিকতা।
তনিমাকে আমি শক্ত করে জড়িয়ে আছি ঠিকই। তবে ইচ্ছে করছে আজ একবার বাপানের কাছে যাই। আজ না হয় কাল… ক’দিন ওর সঙ্গেই রাতে শোবো। বিরক্ত হয় হোক।
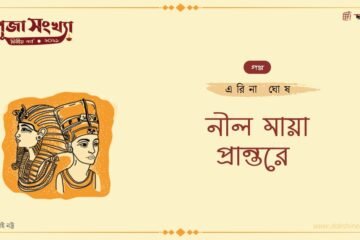


0 Comments